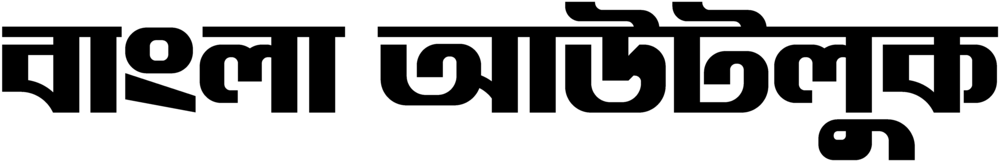ছবি: সংগৃহীত
এই সিরিজটির প্রথম পর্বে আমরা দেখেছি সিসন এবং রোজ তাদের ‘War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh’ বইয়ে বাংলাদেশের জন্ম নিয়ে কি লিখেছেন, এবং দ্বিতীয় পর্বে গ্যারি জে ব্যাসের ‘The Blood Telegram: Nixon, Kissinger and a forgotten genocide’এর উপর আলোচনা আমরা শেষ করি এই বলে যে ১৯৭১ সালে ভারতের পদক্ষেপগুলির বিশ্লেষণ একটি আকর্ষণীয় পাঠ হবে।
সমানভাবে আকর্ষণীয় হবে প্রাথমিক এবং উপক্রমিক বিশ্বায়নের আলোকে বাংলাদেশের যুদ্ধের একটি বিশ্লেষণ। বিশ্বায়ন বলতে এখানে আমি শুধু বহুজাতিক কর্পোরেশন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং পুঁজি প্রবাহের মতো অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বোঝাচ্ছি না। গত শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশক ছিল এমন এক সময় যখন : উপনিবেশোত্তর নব্য স্বাধীন দেশগুলো থেকে মানুষ কাজের জন্য প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে গিয়ে এক অভিবাসী সমাজের গোড়াপত্তন করতে শুরু করে; অলাভজনক বেসরকারি সংগঠন – NGO – কার্যক্রম শুরু হয় সেইসব দেশে যেখানে রাষ্ট্র ছিল অনুপস্থিত এবং সমাজ মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিল সংকট। শুরু হয় ব্যক্তি অধিকারের উপর ভিত্তি করে রাজনীতির নতুন রূপ যা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের ভারী হাত নয় বরং দীর্ঘ দিনের সামাজিক নিপীড়নকেও চ্যালেঞ্জ করে; এবং প্রতিসংস্কৃতি, রক সঙ্গীত, এবং পপ আর্ট-এর মতো সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রবণতা এবং নতুন অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রযুক্তি যা বিশ্বব্যাপী নতুন প্রজন্মের আন্দোলনের গতি প্রকৃতিই বদলে দিয়েছিলো।
এই প্রবণতাগুলির প্রত্যেকটি বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের আগে এবং পরে উভয় ক্ষেত্রেই ভূমিকা পালন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, পূর্ব লন্ডনের বাঙালি প্রবাসীদের বাংলাদেশের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভারতে শরণার্থীদের জন্য ত্রাণ প্রচেষ্টার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পর্কে অনেকেই জানি। কিন্তু ১৯৭১এর আগের দশকে যুক্তরাজ্য ছিল রেহমান সোবহান, মওদুদ আহমেদ, শফিক রেহমান, কামাল হোসেন এবং ফজলে হাসান আবেদের মতো ব্যক্তিদের জন্য তাদের ধারণাগুলি ধারালো করার একটি শিক্ষামূলক পরিবেশ। শেষোক্ত ব্যক্তি যুদ্ধের পরে বাংলাদেশ পুনর্বাসন সহায়তা কমিটি (ব্র্যাক) প্রতিষ্ঠা করেন, যা শেষ পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম এনজিওতে পরিণত হয়। অন্যরা দেশের গঠনমূলক বছরগুলিতে ছিলেন সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ পদে, কাজ করেছিলেন স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারগুলির অধীনে অর্থনৈতিক আমলাতন্ত্র ও নীতি নির্ধারণ, মিডিয়া এবং রাজনীতিতে।
১৯৭১ সালে, আন্তর্জাতিক সচেতনতা শুধুমাত্র পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও দূতাবাসের করিডোর নয়, বরং জনপ্রিয় মিডিয়ার অভিনব ব্যবহারের মাধ্যমে, সক্রিয়কর্মীরা সরাসরি পশ্চিমা জনমতকে লক্ষ্য করেছিল। আখেরে, Concert for Bangladesh ইতিহাসে এই ধরনের প্রথম অনুষ্ঠান ছিল! বব ডিলান বা দ্য বিটলস বলি, কিংবা চে গুয়েভারা বা চেয়ারম্যান মাও—তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানি তারুণ্যের কাছে এগুলো কিছুই অজানা ছিল না, এবং ১৯৬৮ (soixante-huitard) এর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলো তারা আয়ুব খানের বিরুদ্ধে সাফল্যজনক বিদ্রোহের মাধ্যমে।
শুধুমাত্র বিখ্যাত এবং চাকচিক্যপূর্ণ ব্যক্তিরাই নয় যারা বাংলাদেশে নৃশংসতার অবসানের জন্য জোরালো দাবি করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাচেল স্টিভেন্সের সাম্প্রতিক গবেষণা দেখায় যে অস্ট্রেলিয়ার শহরতলীর বাসিন্দারা, যাদের সাথে বাংলাদেশি জনগণ এবং অস্ট্রেলীয় সরকার কারোর সাথেই খুব একটা যোগাযোগ ছিল না, তারা কিভাবে একটি বাংলাদেশের সমর্থনের আন্দোলন শুরু করেন যা ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকের বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন এবং আমাদের নিজের সময়ের জলবায়ু সক্রিয়তার পূর্বাভাস দিয়েছিল।*
নয়া দিল্লি ভিত্তিক পণ্ডিত শ্রীনাথ রাঘবন তার 1971: a Global History of the Creation of Bangladesh বইতে প্রবাসী, এনজিও, পপ কালচার এবং নাগরিক সক্রিয়তার বৈশ্বিক প্রবণতাগুলি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তারপরেও, বইটির নামকরণ একটু ভুল বলে মনে করা যেতেই পারে এই অর্থে যে রাঘবন এই বৈশ্বিক মাত্রাগুলির কোনোটিতেই গভীরভাবে প্রবেশ করেননি—যা কিচ্ছু সরাসরি জাতিরাষ্ট্রগুলির সাথে সম্পর্কিত নয়, সেগুলোর কিছু নিয়েই তিনি গভীর ভাবে কিছু বলেননি। বরং, বৈশ্বিক নাম সত্ত্বেও, তার ফোকাস হল আন্তর্জাতিক—অর্থাৎ, জাতি-রাষ্ট্রগুলির সংক্রান্ত বিষয় এবং কার্যকলাপ— প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ সালের বিবরণ।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নব্য স্বাধীন বিশ্বে যে নেহরু-নাসের-টিটোর আদর্শবাদ ছিল, ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে তা পর্যবসিত হয়েছিল বেশিরভাগ দেশেই সামরিক বা বেসামরিক স্বৈরাচারী শাসনে। এই সরকারগুলির বেশিরভাগেরই বাংলাদেশের বিষয়ে খুব একটা সহানুভূতি ছিল না। ততদিনে শীতল যুদ্ধ “ceased to be a simple bipolar contest”—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক মিত্র উন্নয়নশীল বিশ্বে তাদের নিজস্ব এজেন্ডা চালু করেছিল। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণচীন বিশ্বের দীর্ঘতম স্থল সীমান্ত জুড়ে একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। সেই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের বিপরীতে, রাঘবন যুক্তি দেন যে “there was nothing inevitable about the emergence of an independent Bangladesh in 1971” (“১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব সম্পর্কে কিছুই অনিবার্য ছিল না”)।
স্বীকার করতে বাধ্য যে এই ব্যক্তিগতভাবে এই তত্ত্বটি আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয়। কিন্তু রাঘবন কি আসলে একটি বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি উপস্থাপন করেন যে “the creation of Bangladesh was the product of conjuncture and contingency, choice and chance” ("বাংলাদেশের সৃষ্টি ছিল সংযোগ ও আকস্মিকতা, পছন্দ ও সুযোগের ফসল")?
রাঘবনের কাছে সিসন এবং রোজের মতো মূল সাক্ষাৎকারের উপায় ছিল না। হোয়াইট হাউস টেপের মতো কিছুও তার কাছে ছিল না। মূলত ভারতীয় এবং পশ্চিমা আর্কাইভাল উৎস এবং বিদ্যমান সাহিত্য বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে, রাঘবন রাস্তার কয়েকটি সম্ভাব্য বাঁকের দিকে ইঙ্গিত করেন যেখানে একটি ভিন্ন পথ নেওয়া যেতে পারত। কিন্তু এই সমস্ত বিকল্পগুলি সমানভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা তার এই দাবিটি নিয়ে চিন্তা করি: “…if Bhutto had not worked with the military regime…. a united Pakistan could have been preserved” ( "...যদি ভুট্টো সামরিক শাসনের সাথে কাজ না করতেন.... একটি সংযুক্ত পাকিস্তান সংরক্ষণ করা যেতে পারত")। যদিও এটি সংকীর্ণ অর্থে সত্য হতে পারে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে এটি একটু সরলয়করণ, কারণ আমরা সিসন এবং রোজ থেকে জানি যে ভুট্টোর চাল সর্বদাই ছিল সেনাবাহিনীকে পূর্বে একটি যুদ্ধে উৎসাহিত করা যার শেষে তিনি পশ্চিমে শাসন করবেন।
একটি আরও বলিষ্ঠ যুক্তি, ব্যাসের প্রতিধ্বনি করে, হতে পারে যে যদি আমেরিকানরা “had used .. economic leverage … Yahya … would have been forced to negotiate with Mujib” ("অর্থনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করত ... ইয়াহিয়া ... মুজিবের সাথে আলোচনা করতে বাধ্য হতেন")।
কিন্তু আমেরিকানরা কি সত্যিই পাকিস্তানি কার্যকলাপকে প্রভাবিত করতে পারত?
এই শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে, দুই খুবই ভিন্ন রাষ্ট্রপতির অধীনে খুবই ভিন্ন বৈদেশিক নীতি দর্শনের আলোকে, আমেরিকা তার বেশিরভাগ মিত্রদের সমর্থন ছাড়াই একটি আরব দেশ আক্রমণ করে এবং তার একনায়ককে হত্যা করে, তারপর তার মিত্রদের তাগিদে অনিচ্ছাকৃতভাবে আরেকটি আরব দেশকে বোমা হামলা করে এবং বিদ্রোহীদের অস্ত্র দেয় যারা তার একনায়ককে হত্যা করে, এবং অন্য একটি আরব দেশে আরেকজন একনায়কের বিরুদ্ধে একটি জনপ্রিয় বিদ্রোহ যখন এই তরুণ শতাব্দীর সবচেয়ে খারাপ যুদ্ধগুলির একটিতে পর্যবসিত যায় তখন কিছুই করে না। এটি মোটেও স্পষ্ট নয় যে মার্কিন ক্ষমতা— যেভাবেই ব্যাবহার হোক বা না হোক – ইরাক, লিবিয়া, এবং সিরিয়ার জনগণের জন্য কোনো ভালো কিছু এনেছে। আমরা কীভাবে এত আত্মবিশ্বাসী হতে পারি যে একটি শক্তিশালী আমেরিকান অবস্থান বাংলাদেশের জনগণের জন্য ভালো হত?
ভিন্নভাবে বলতে গেলে, এমনকি যদি আমরা মেনেও নেই যে কিসিঞ্জার এবং নিক্সন ১৯৭১ সালে একটি ত্রুটিপূর্ণ ও ব্যর্থ নীতি অনুসরণ করেছিল, এর অর্থ এই নয় যে মার্কিন কর্মকাণ্ড তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ভালো কিছু হতোই। সেই যুক্তি সাব্যস্ত করার করার জন্য দরকার পূর্ব পাকিস্তানি এবং বাংলাদেশি রাজনীতির একটি বিশ্লেষণ, যা চিহ্নিত করবে ঢাকায় আমেরিকা-সমর্থক রাজনীতিবিদ এবং গোষ্ঠীগুলি এবং ক্ষমতা প্রয়োগের তাদের বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা। যেমনটা, আমরা জানি যে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, আমেরিকানদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। মোশতাক যুদ্ধের আগে আওয়ামী লীগের পশ্চিমা-সমর্থক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতেন বলে পরিচিত ছিলেন। এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময়ও, লীগকে পশ্চিমা মিডিয়া দ্বারা পাকিস্তানের যেকোনো অঙ্গের প্রধান পশ্চিমা-সমর্থক দল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।
অর্থাৎ, ঢাকায় ক্ষমতার গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বীএক দল ছিল যাদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও একটি সম্ভাব্য অংশীদার ছিল, সমালোচিত আধিপত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও। যদি আমেরিকানরা ইয়াহিয়াকে স্পষ্ট করে দিত যে তারা আওয়ামী লীগের সাথে কাজ করবে, তাহলে জেনারেল কি চাপের কাছে নতি স্বীকার করতেন? এবং যদি তিনি না করতেন, তাহলে কি অন্য কোনো জেনারেল থাকতে পারত যার সাথে আমেরিকানরা কাজ করতে পারত?
লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহিবজাদা ইয়াকুব খান একটি কৌতূহলী উদাহরণ হতে পারেন । তিনি ছিলেন অপেক্ষাকৃত হার্ডলাইনার হিসেবে পরিচিত, তিনি ছিলেন কুখ্যাত অপারেশন সার্চলাইট — ২৫-২৬ মার্চের সামরিক দমনের স্থপতি । কিন্তু প্রদেশের সামরিক গভর্নর হিসেবে মার্চের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় পৌঁছে, তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে একটি সামরিক সমাধান কাজ করবে না। তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে ফিরে যান, এবং পরবর্তীতে আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্বের সময় জিয়া-উল-হক এবং বেনজির ভুট্টোর অধীনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আমেরিকান চাপের অধীনে কি একটি ইয়াকুব শাসন শেখ মুজিবকে ছাড় দিতে পারত?
এটি, অবশ্যই, শুধুমাত্র অনুমান। কিন্তু এটি এমন ধরনের অনুমান যা অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চাই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাব বিস্তার করতে পারত এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিতে পারত।
ব্যাস এবং রাঘবন উভয়ই পরোক্ষভাবে দাবি করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭১ সালে ভালোর জন্য ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করতে পারত। কিন্তু কেউই পাকিস্তানে পশ্চিমা-সমর্থক গোষ্ঠীগুলির কোনো বিশ্লেষণ দিয়ে দাবিটি সমর্থন করেননি।
(চলবে)
*Rachel Stevens, “Humanitarianism from the Suburbs: Australian refugee relief and activism during the 1971 Bangladeshi Liberation War”, Australian Journal of Politics and History, 2019.