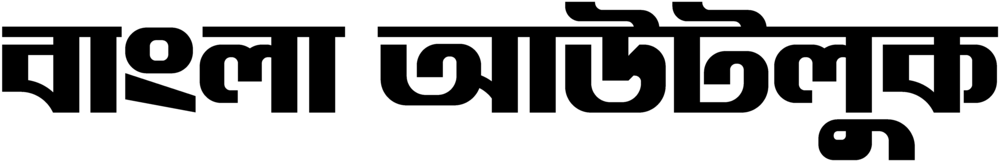মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যা জানা গিয়েছে, যা জানা সম্ভব
ড. তৌফিক জোয়ার্দার
প্রকাশ: ২০ এপ্রিল ২০২৫, ০৮:২৫ পিএম
-680503f44f6c0.jpg)
এক মহান যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশটি স্বাধীন হয়েছে। এর পেছনে রয়েছে অসংখ্য মানুষের অপরিসীম আত্মত্যাগ। নানা সূত্র থেকে আমরা শুনে এসেছি ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমাদের এ স্বাধীনতা। অনেকেই আবার ৩০ লক্ষ শহীদের সংখ্যাটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এমন প্রশ্ন ওঠার মূলে রয়েছে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে ৭১-পরবর্তী শাসকদের উদাসীনতা। তারা এত বছরেও শহীদের সংখ্যা নির্ণয়ে আন্তরিকভাবে কোনো গবেষণা করেননি। আর এ বিষয়ে যদি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী অবিমৃশ্য ও অপ্রয়োজনীয় মিথ্যাচার করেই থাকেন, তাহলে সেই মিথ্যার সূত্র ধরে ভবিষ্যতে অনেক জ্বলন্ত সত্যও প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। তাই এটা নিয়ে গবেষণা করে বিতর্ক ঘোচানোর পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, আজ এত বছর পরে এ বিতর্ক নিরসনের বৈজ্ঞানিক কোনো পদ্ধতি আদৌ আছে কিনা।
যুদ্ধ বা গণহত্যায় মৃতের সংখ্যা নির্ণয়ের যেসব পদ্ধতি আছে, সেগুলোকে মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হলো বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত রিপোর্টের ভিত্তিতে। একে বলা হয় প্যাসিভ সার্ভিলেন্স পদ্ধতি বা রিপোর্ট রিভিউ পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো যুদ্ধের পূর্বের এবং পরের মৃত্যুহার তুলনা বা জনমিতিক মডেলিং। তৃতীয় পদ্ধতিটি হলো ভূতাপেক্ষ মৃত্যুহার জরিপ অথবা মৃত্যু শুমারি। এই প্রত্যেকটি পদ্ধতিই আবার নানা ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ সবগুলোরই আছে সুবিধা এবং অসুবিধার দিক। নিচে এ পদ্ধতিগুলোর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রয়োগ, বাংলাদেশে এর প্রয়োগ ও ফলাফল, সুবিধা-অসুবিধার দিক এবং বাংলাদেশে নতুন ও উন্নততর মেথডোলজি ব্যবহার করে এটিকে কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।
ক. রিপোর্ট রিভিউ বা প্যাসিভ সার্ভিলেন্স:
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রয়োগ ও সুবিধা-অসুবিধা:
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এর প্রয়োগের সবচেয়ে বিখ্যাত যে উদাহরণটি রয়েছে তা হলো ইরাক বডিকাউন্ট স্টাডি (সূত্র: www.iraqbodycount.net)। এ সংগঠনটি ইরাক যুদ্ধের শুরু থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যার হিসাব রাখা শুরু করে। এ পদ্ধতিতে তারা যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজারের মধ্যে বলে দাবি করে। পত্রপত্রিকার খবর ছাড়াও এ পদ্ধতিতে আরো নানা রিপোর্টের ওপর নির্ভর করা হয়, যেমনটি করা হয়েছিল বসনিয়া-হার্জেগোভিনার গণহত্যায় মৃতের সংখ্যা নিরুপনেও। সেখানে পত্র পত্রিকার বাইরেও পর্যালোচনা করা হয়েছিল গণকবর খুঁড়ে বের করা কঙ্কালের সংখ্যার রিপোর্ট, হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের খোঁজে করা ডায়রি, সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রকাশিত তাদের সৈনিকদের মৃত্যুর নোটিফিকেশন, মর্গের রিপোর্ট, কবরস্থানের রিপোর্ট, হাসপাতাল রিপোর্ট ইত্যাদি। এ পদ্ধতির একটি বড় সমালোচনা হলো, পত্রপত্রিকায় অনেক সময়ই রাজনৈতিক বিবেচনায় মৃতের সংখ্যা বাড়িয়ে বা কমিয়ে প্রকাশ করা হয়। বলাই বাহুল্য, তাই এ পদ্ধতিতে প্রচুর ভুলের সম্ভাবনা থাকে। Journal of Conflict Resolution এর ডিসেম্বর ২০০৯ এ প্রকাশিত ৫৩ (৬) সংখ্যার Estimating war deaths: an arena of contestation নিবন্ধে মাইকেল স্পাগাট, এ্যান্ড্রু ম্যাক, টারা কুপার এবং জোয়াকিম ক্রয়েট্জ এই পদ্ধতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "[R]eport-based estimation methods systematically undercount death tolls because large numbers of deaths go unreported." অর্থাৎ, "এ পদ্ধতিটি নিয়মমাফিক ভাবে মৃতের সংখ্যাকে অবমূল্যায়ন করে, কারণ (এ পদ্ধতিতে) বিপুল সংখ্যক মৃত্যু অগোচরে থেকে যায়"।
বাংলাদেশে এর প্রয়োগ হয়ে থাকলে তার ফলাফল:
সুইডেনেরে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নরওয়ের অসলো শহরে অবস্থিত Peace Research Institute ১৯০০ সাল থেকে ঘটে যাওয়া violent death বা হিংসাত্মক মৃত্যু, তথা যুদ্ধ বা গণহত্যা জনিত মৃত্যুর একটি ডেটাবেজ তৈরি করছে। এর জন্য তারা মূলতঃ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নানা রিপোর্টের আশ্রয় নেয়। যেসব দেশের যুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা এখানে রেকর্ড করা হয়েছে তার মধ্যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অন্যতম। ২০০৮ সালে জিয়াদ ওবারমায়ার, ক্রিস্টোফার মারে এবং এমানুয়েলা গাকিদু ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia: analysis of data from world health survey programme শিরোনামে একটি বহুল আলোচিত গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এই নিবন্ধে তাঁরা ১৩ টি দেশের যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা হিসেব করেন এবং উল্লিখিত Peace Research Institute এর ডেটাবেজের সাথে তাঁদের গবেষণার ফলাফল তুলনা করেন। এই ১৩ টি দেশের একটি ছিল বাংলাদেশ; সেই সূত্রে ডেটাবেজে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে মৃতের সংখ্যাটিও এই নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। সংখ্যাটি হলো ৫৮ হাজার। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালের নিবন্ধে গবেষকগণ এ সংখ্যাটির কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং প্রকৃত মৃত্যুসংখ্যাকে নিদেনপক্ষে এর তিন গুণ বলে দাবি করেছেন।
বাংলাদেশে এ পদ্ধতির উন্নততর সংস্করণ প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব:
বাংলাদেশে নতুন করে এ পদ্ধতির প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হবেনা। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা এতটাই অনুন্নত ছিল যে, সে সময় দেশের আনাচে কানাচে ঘটে যাওয়া গণহত্যায় ও যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা যথাযথভাবে পত্রিকায় আসতে পেরেছে বলে মনে হয় না। উপরন্তু, তখনো ঢাকা পশ্চিম পাকিস্তানের আওতায় থাকায় ঢাকা-কেন্দ্রিক পত্রপত্রিকায় যুদ্ধের খবর নিরপেক্ষ ভাবে এসেছে এমনটি ভাবার কারণ নেই। আর স্বাধীনতার পরে বিষয়টি নিয়ে নানামুখী রাজনীতি শুরু হয়ে যাওয়ায় তখনকার পত্র পত্রিকায় রাজনীতিবিদদের মুখের কথাকেই প্রামাণ্য ধরে রিপোর্ট করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অনেকে ১৯৭২ সালের ৩রা জানুয়ারি তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত প্রাভদা পত্রিকার ৩ (১৯৫১ ১) সংখ্যার 'They could not hide it: the real scale of Pakistani government terror in East Bengal becomes evident' রিপোর্টটিকে রেফারেন্স হিসেবে দাখিল করে। সেই রিপোর্টটির ইংরেজি অনুবাদ হলো: "The terror was abysmal in the very Eastern part of Bengal, and as newspapers inform now, more than 3 million people were killed, injured, disabled and imprisoned". অর্থাৎ: "পূর্ব বাংলায় সন্ত্রাস ছিল অতলান্তিক, এবং সংবাদপত্র থেকে যা জানা যাচ্ছে, ৩০ লক্ষেরও অধিক মানুষ মারা গিয়েছে, আহত হয়েছে, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে এবং কারাবরণ করছে"। রিপোর্টটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, এখানেও কোনো বৈজ্ঞানিক জরিপের রেফারেন্স নেই, বরং স্থানীয় পত্রপত্রিকাকেই রেফার করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, ৩০ লক্ষ সংখ্যাটি শহীদের নয়, বরং নিহত, আহত, প্রতিবন্ধীত্ব, এবং কারা বরণকৃত মানুষের সামষ্টিক সংখ্যা। কাজেই রিপোর্টের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নির্ণয়ের প্রচেষ্টা সমর্থনীয় নয়।
খ. জনমিতিক মডেলিং:
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রয়োগ ও সুবিধা-অসুবিধা:
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ দেখা যায় ক্যাম্বোডিয়ার খেমাররুজদের গণহত্যা এবং পূর্ব তিমুরের গণহত্যায় নিহতদের সংখ্যা নিরূপণে। এ পদ্ধতির সুবিধা হলো, এতে অনেক অর্থ ব্যয় করে জরিপ চালানোর প্রয়োজন পড়েনা; বিদ্যমান জনমিতিক তথ্য বা আদম শুমারি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে যুদ্ধের আগে অশোধিত মৃত্যু হার (crude death rate) জেনে নেওয়া হয়। যুদ্ধের পরপর হলে একটি জরিপ চালিয়ে যুদ্ধকালীন সময়ের মৃত্যুহার ও মৃত্যু সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। যুদ্ধের পূর্বের হার অনুযায়ী সেই সময়ে মৃত্যুর সংখ্যা কত হতে পারতো (projected number of death) তা নির্ণয় করা হয়। Projected number of death থেকে জরিপ থেকে প্রাপ্ত actual number of death বিয়োগ করে যুদ্ধ-জনিত মৃত্যুর সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। এ পদ্ধতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে কেবল সরাসরি যুদ্ধের কারণে মৃত্যুই নয়, বরং যুদ্ধের ফলাফল স্বরূপ যে অতিরিক্ত মৃত্যু(excess death) হয়ে থাকে তাও নির্ণয় করা যায়। যেমন: যুদ্ধের কারণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে; যার ফলশ্রুতিতে প্রসূতির মৃত্যু হলে কিংবা কোনো সংক্রামক রোগে মানুষ মারা গেলে, এমনকি দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অপুষ্টিতে ভুগে কেউ মারা গেলেও তা গবেষণায় ধরা পড়ে। তবে এর অসুবিধাটি হলো, অনেক সময়ই যুদ্ধের পূর্বের জনমিতিক তথ্য পাওয়া যায় না। অনেক সময় এসব তথ্য অসম্পূর্ণ থাকে বা একদম গ্রাম বা উপজেলা ভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় সমস্যা হলো গবেষণাটি যুদ্ধের অনেক বছর পরে করা হলে কিংবা যুদ্ধটি দীর্ঘদিন ধরে চললে অনুস্মরণ কাল (recall period) বেশি হওয়ায় অনুস্মরণ পক্ষপাত (recall bias) সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ, মৃত্যুর সঠিক সংখ্যাটি মানুষের মনে নাও থাকতে পারে। তবে উপস্থিত তথ্য থেকেও advanced modeling এর মাধ্যমে, গুরুত্বপূর্ণ confounder গুলোকে চিহ্নিত করে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে, এসব উপাত্ত থেকেও একটি দীর্ঘ আস্থা ব্যবধানের (confidence interval) মধ্যে মৃতের সংখ্যা অনুমান করা সম্ভব।
বাংলাদেশে এর প্রয়োগ হয়ে থাকলে তার ফলাফল:
বাংলাদেশে এধরনের একটি গবেষণা করেছিল আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ। মতলব বাজার এলাকায় করা গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক জার্নাল Population Studies এ। George T Curlin, Lincoln C Chen, এবং Sayed Babur Hossain এর গবেষণা নিবন্ধটির নাম Demographic crisis: the impact of the Bangladesh civil war (1971) on births and deaths in a rural area of Bangladesh'। এটি ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষের জনমিতিক উপাত্তের ওপর নির্ভর করে করা, যেখানে ১৯৬৬-৬৭ সালের সাথে ১৯৭১-১৯৭২ সালের জনসংখ্যার তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে যুদ্ধের মৃত্যুসংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। Population Science এর ৩০ (১) সংখ্যার ৮৭-১০৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্ত রিপোর্টটিতে উল্লেখ করা হয়েছে: "Accepting these limitations, it appears useful to estimate the probable overall demographic impact of the war on Bangladesh. Assuming a national population of 70 million in 1971-72 and the Matlab Bazar base vital rates, ....[w]ith increases in the death rate in 1971-72 .... of 40 ...per cent ...., this implies an overall excess number of deaths of nearly 500,000. By any standard this was a major disaster." অর্থাৎ, "সীমাবদ্ধতা গুলোকে স্বীকার করে নিয়েও, বাংলাদেশের ওপর যুদ্ধের সামগ্রিক প্রভাব নির্ণয়ে গবেষণাটি কাজে লাগতে পারে। ১৯৭১-১৯৭২ সালে জনসংখ্যা ৭ কোটি ধরে নিয়ে, মতলব বাজারের জনমিতিক হার গুলোকে প্রামাণ্য ধরে নিয়ে, এবং ১৯৭১-১৯৭২ সালের ৪০% (যুদ্ধের কারণে) বাড়তি মৃত্যু হারকে (উক্ত গবেষণা থেকে প্রাপ্ত) আমলে নিলে, (যুদ্ধের কারণে) অতিরিক্ত মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৫ লক্ষ। যে কোন মানদণ্ডে এটি একটি গুরুতর বিপর্যয়।"
বাংলাদেশে এ পদ্ধতির উন্নততর সংস্করণ প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব:
বাংলাদেশে আবারো এ ধরনের গবেষণা করা সম্ভব, তবে দীর্ঘ সময় পার হয়ে যাওয়ায় অনুস্মরণ কাল অনেক বেশি হবে এবং জরিপের ফলাফল প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। তবে সেই সময় আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন সংস্থা এ ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করেছিল কিনা খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে। সেই সময় বাংলাদেশে যেসমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা কাজ করছিল তাদের সাথে যোগাযোগ করে দেখা যেতে পারে, যেমন ইউনিসেফ। তাছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাছেও গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত থাকতে পারে।
গ. ভূতাপেক্ষ মৃত্যুহার জরিপ অথবা মৃত্যু শুমারি
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রয়োগ ও সুবিধা-অসুবিধা:
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ পদ্ধতির সবচেয়ে আলোচিত প্রয়োগটি ঘটেছিল ইরাক যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা নির্ণয়ে; যা মার্কিন সরকারকে দারুণভাবে বিব্রত করেছিল। রিপোর্ট রিভিউ বা প্যাসিভ সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে পূর্বের নির্ণয় করা এবং মার্কিন সরকার কর্তৃক প্রচারিত সংখ্যার চাইতে ২০০৬ সালে ভূতাপেক্ষ জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত সংখ্যাটি ছিল প্রায় ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার বেশি। লে রবের্তস, রিয়াদ লাফতা, রিচার্ড গারফিল্ড, জামাল খুদাইরি এবং গিলবার্ট বার্নহ্যামের দলটি মাল্টিস্টেজ ক্লাস্টার র্যান্ডম স্যাম্পলিং করে গোটা ইরাক থেকে দ্বৈবচয়নের মাধ্যমে ৩৩ টি ক্লাস্টার বেছে নিয়েছিলেন। একেকটি ক্লাস্টার থেকে ৩০ টি খানায় জরিপ করা হয়েছিল। খানা জরিপের মাধ্যমে মার্কিন দখলদারিত্বের ১৭.৮ মাস সময়ের মৃত্যু হারের সাথে এর পূর্ববর্তী ১৪.৬ মাসের মৃত্যু হার তুলনা করে, যুদ্ধের মৃতের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়েছিল এক মিলিয়ন বা ১০ লক্ষ। বাংলাদেশে এ পদ্ধতি সরাসরি প্রয়োগ করা সমস্যাজনক হবে দীর্ঘ সময়ের কারণে অনুস্মরণ পক্ষপাতের সম্ভাবনার কারণে। তবে এখানে করা নমুনায়ন পদ্ধতি (sampling method) আমাদের জন্য দিকনির্দেশনা দিতে পারে। এরকম আরেকটি গবেষণা হলো ফিলিপ ভেরউইম্পের Death and survival during the 1994 genocide in Rwanda, যা প্রকাশিত হয়েছে Population Studies জার্নালে ২০০৪ সালে ৫৮ (২) সংখ্যায়। সেখানে রুয়ান্ডার কিবুইয়ে জেলার বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটি মৃত্যু রেজিস্ট্রার তৈরি করা হয়, যা ঐ জেলায় ৫৯,০৫০ টি মৃত্যু শনাক্ত করে। এই হারকে অন্যান্য এলাকায় প্রয়োগ করে মোট মৃতের সংখ্যা অনুমান করা হয়।
বাংলাদেশে এর প্রয়োগ হয়ে থাকলে তার ফলাফল:
এ ধরনের একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল ২০০২-২০০৩ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার জন্য করা বিশ্ব স্বাস্থ্য জরিপের অংশ হিসেবে। সেখানে সহোদর ইতিহাস জরিপের (sibling history survey) মাধ্যমে ৫৫১৫ খানার ৩৬৬২৭ সহোদরের ওপর করা জরিপের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে মৃতের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। ২০০৮ সালে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত জিয়াদ ওবারমায়ার, ক্রিস্টোফার মারে এবং এমানুয়েলা গাকিদুর Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia: analysis of data from world health survey programme শীর্ষক এ গবেষণা নিবন্ধে মৃতের সংখ্যা নির্ণয় করা হয় ২ লক্ষ ৬৯ হাজার। ৯৫% আস্থা ব্যবধানের ভিত্তিতে মৃতের সংখ্যা সর্বনিম্ন ১ লক্ষ ২৫ হাজার এবং সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ ৫ হাজার হতে পারে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। সহজ ভাষায় বললে, এই গবেষণাটি ১০০ বার করলে ৯৫ বারই শহীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার থেকে ৫ লক্ষ ৫ হাজারের মধ্যে পাওয়া যাবে।
বাংলাদেশে এ পদ্ধতির উন্নততর সংস্করণ প্রয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব:
বাংলাদেশের জন্য ভূতাপেক্ষ মৃত্যুহার জরিপ অথবা মৃত্যু শুমারি (সেন্সাস) বা এ ধরনের পদ্ধতি উপযুক্ত; যদিও এর সাথে সাথে সামাজিক মানচিত্রায়ন (social mapping) পদ্ধতিরও সংযোগ ঘটাতে হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সেন্সাস পদ্ধতি নানা কারণে একটি ভাল পদ্ধতি। প্রথমত: বাংলাদেশে এমন কোনো যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে না যার দরুন দেশের কোনো অংশ অগম্য। দ্বিতীয়ত: বিষয়টি দেশের আত্মপরিচয়ের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, তাই সেন্সাসের মতো একটি ব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে সমর্থনীয়। তৃতীয়ত: আমাদের দেশের ভৌগোলিক প্রতিবেশ, জনসংখ্যার ঘনত্ব, সামাজিক সুসংগতি এবং এক স্থান থেকে আরেক স্থানের স্বল্প দূরত্ব সেন্সাস পদ্ধতিকে খুবই সম্ভবপর প্রতীয়মান করে। তবে একথা সত্য যে, সেন্সাস একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল উদ্যোগ। সরকারের আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার ছাড়া এটি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।
এখানে পরিষ্কার করে রাখা ভালো যে, যে কোনো যুদ্ধে সরাসরি সহিংস মৃত্যুর বাইরেও যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল হিসেবে অতিরিক্ত মৃত্যু (exceess death) হতে পারে। এ নিয়ে সম্প্রতি কৌস্তুভ অধিকারী, নাজমুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান জালাল PLOS One জার্নালে Death toll among the Bangladesh refugees of the 1971 war শিরোনামের নিবন্ধে শরণার্থীদের মধ্যে যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত মৃত্যুসংখ্যা ৫,৬২,৯১৫ বলে হিসেব করেছেন। এদিকে শাহাদুজ্জামান এবং খায়রুল ইসলাম দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সালে প্রকাশিত ’১৯৭১ সালে শরণার্থী শিবিরে মৃতের সংখ্যা কত’ নিবন্ধে সংখ্যাটি ৩,১৭,৫৩৯ বলে প্রাক্কলন করেছেন। জানিয়ে রাখা ভালো, আমার নিবন্ধে যে সংখ্যাটি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে তা যুদ্ধের সহিংস মৃত্যুর, যা দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। এখানে শরণার্থী শিবিরের মৃত্যুকে হিসেবে নেওয়া হয়নি, যদিও সেটিও নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।
ওপরের আলোচনা থেকে আমরা দু’টি গুরুত্বপূর্ণ উপসংহারে আসতে পারি। এক, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন আছে। দুই, এই প্রশ্ন নিরসনের বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি আছে, যার মাধ্যমে এখনো শহীদের সংখ্যাটি নিরূপণ করা সম্ভব। এর জন্য কেবল প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা। এখনো এ সংখ্যাটি নির্ণয় করা সম্ভব; তবে আরো কিছু বছর পেরুলে তা আর সম্ভব নাও হতে পারে। আমাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ আবেগের বিষয়, কিন্তু তাই বলে এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে পারবেনা এমন কথা নেই, বরং শহীদদের সংখ্যা নিয়ে যেন ভবিষ্যতে কেউ রাজনীতি করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্যই এটি প্রয়োজন।
ড. তৌফিক জোয়ার্দার, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরের সহযোগী অধ্যাপক