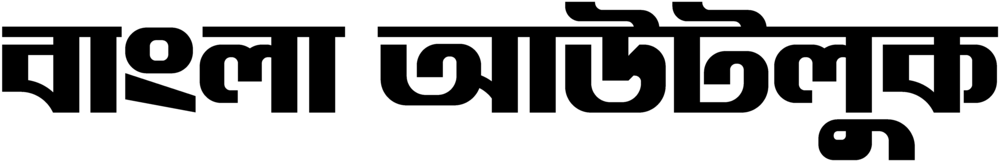নির্বাচন নাকি সংস্কার? কিছু তাত্ত্বিক আলাপ

গণতন্ত্র নাকি উন্নয়ন? আওয়ামী ফ্যাসিবাদী আমলের এই জঘন্য বাইনারি অপোজিশনের বিরুদ্ধে সবসময় আমরা সোচ্চার থেকেছি একটা দাবি নিয়ে সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র এবং উন্নয়ন কোনোটা কোনোটার বিকল্প নয়, বরং এগুলো একে অন্যের পরিপূরক।
আর সে হিসেবে গণতন্ত্র যেমন প্রয়োজন মানবিক মর্যাদা ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তেমনি উন্নয়ন প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব। যদি তারা এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে পাঁচ বছর পর জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অথর্ব ও ব্যর্থ সরকারকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।
যদি এদিক থেকে চিন্তা করে দেশে গণতন্ত্র থাকলে সরকার উন্নয়ন করতে বাধ্য হবে। আর গণতন্ত্রকে হ*ত্যা করে কেউ যদি উন্নয়নের গান গায় তবে বুঝতে হবে তারা উন্নয়ন নয় লুটপাট করার পূর্ণ স্বাধীনতা চাইছে। এখানে মুখটা লুটতরাজের, আর মুখোশ হচ্ছে উন্নয়ন।
ফ্যাসিবাদী আমলের লাগাতার বিচারহীনতা, গুম, খুন কিংবা ব্যাংক ডাকাতি সবকিছুর নেপথ্য কারণ গণতন্ত্রকে গলা টিপে মেরে ফেলা। জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জবাবদিহিতার সুযোগ নাই করে দেওয়ায় তখন সরকার হয়ে উঠেছিল স্বেচ্ছাচারী এবং দুর্বিনীত। তারা মুখে গান গেয়েছে উন্নয়নের আর নৃত্য করেছে দুর্নীতি তথা লুটপাটের।
সম্প্রতি নতুন সুরে সেই পুরাতন ফ্যাসিবাদী ডিসকোর্সের ভাঙ্গা রেকর্ড আমরা শুনতে পাচ্ছি। অনলাইনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বট বাহিনী চিরচেনা আওয়ামী সুরে গাইছে ফ্যাসিবাদী রিমেক ‘সংস্কার নাকি নির্বাচন’। আর সেখানেই বাধা আমাদের। আমরা বলতে চাই দেশের জন্য গণতন্ত্র যেমন জরুরি, তেমনি সংস্কারও জরুরি। এখানে একটাকে অন্যটার সরাসরি প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে কেনো?
উপরের এই কথাগুলো লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে কেউ আপনাকে বি এন পি ট্যাগ মারবে? মনে হবে গণতন্ত্র কিংবা মানবিক মর্যাদার দাবি জানানোটা ফ্যাসিবাদী আমলের মতোই বিরাট অপরাধ। তখন আমাদের ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছিল কেনো সেটা সবাই জানে, সেই উন্নয়নের ঘুমপাড়ানি গানে। আর এখন নির্বাচন নিয়ে কথা বলতে গেলেই মুখস্থ সংলাপ বি এন পি সংস্কার চায় না। তারা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে ফ্যাসিবাদ টু পয়েন্ট জিরো কায়েম করতে চায়।
কিন্তু তারা কমবেশি সবাই জানে যে সংস্কার প্রস্তাবনা আসার বহু আগে উপরাষ্ট্রপতি ও উপপ্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করেছিল বিএনপি। দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য, বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার দেওয়ার প্রস্তাব ছিল তাদেরই। ওদিকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সময়সীমা নির্ধারণ বা ক্ষমতা হ্রাসের প্রস্তাবও অন্য কেউ দেয়নি, দিয়েছিল বি এন পি। এই কথাগুলো তারা আমার নতুন করে দিয়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছে।
খেয়াল করলে দেখা যায় কমিশনের দেওয়া অধিকাংশ সুপারিশের সঙ্গেও একমত পোষণ করেছে বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলটি। সম্প্রতি যুগান্তরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সুস্পষ্ট করে বিষয়গুলো জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন। তিনি কোনোরকম রাখ ঢাক বাদে বলেছেন ‘সংস্কারের প্রধান প্রস্তাবক ও ধারক বিএনপি। বর্তমানে যে সংস্কারের কথা উঠছে সেগুলোর অধিকাংশই ৩১ দফায় ছিল। গণভোট ও গণপরিষদের বিরোধিতা করে তিনি বলেন, ৫ আগস্টের আগ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কেউ কথা বলেননি, জনগণেরও ধারণা নেই। আর বিএনপি সংস্কার চায় না-এমন অপপ্রচার চালাচ্ছে একটি গোষ্ঠী, যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’।
গণতন্ত্র নাকি উন্নয়নের পর নতুন হাজির হওয়া ভুতুড়ে গল্প সংস্কার নাকি নির্বাচনের বাস্তবতা বুঝতে আমরা বাইনারি অপোজিশনের তত্ত্বসমূহ একটু পর্যালোচনা করতে পারি। বাস্তবে এই বাইনারি অপোজিশন ধারণাটি এমন শব্দ বা ধারণার জোড়াগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে যা একে অপরের বিপরীতে স্থাপিত। প্রতিটি একক একটি পৃথক, প্রায়ই বিপরীত, ধারণা বা মূল্য প্রতিনিধিত্ব করে। এটি কাঠামোগতবাদী তত্ত্বের একটি মূল ধারণা। বিশেষত ফরাসি নৃবিজ্ঞানী ক্লদ লেভি-স্ট্রস এবং সাহিত্য তত্ত্ববিদদের কাজের মধ্যে, যেমন রঁলা বার্ত এবং জ্যাক দেরিদা এই প্রসঙ্গ বিস্তৃত আলাপনে এনেছেন। উত্তরাধুনিকতায় এডওয়ার্ড সাইদের চিন্তাতেও আমরা এর প্রতিফলন দেখি।
আমরা জানি যে, লেভি-স্ট্রস তার কাঠামোগতবাদী পদ্ধতির একটি অংশ হিসেবে বাইনারি অপোজিশনের ধারণাটি তৈরি করেছিলেন। তিনি মিথ এবং সাংস্কৃতিক প্রথাগুলোর বিশ্লেষণে বাইনারি অপোজিশনের ব্যবহৃত হওয়ার প্রতি আলোকপাত করেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে মানব মস্তিষ্ক বিশ্বের বিভিন্ন অংশকে বিপরীত জোড়ায় শ্রেণিবদ্ধ করতে সহজাত প্রবৃত্তির ভিত্তিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। যেমন জীবন/মৃত্যু, ভাল/খারাপ, প্রকৃতি/সংস্কৃতি প্রভৃতি। তিনি এই বাইনারি কাঠামোগুলো মিথ, আচার-অনুষ্ঠান, এবং সংস্কৃতির কাহিনি এবং নির্মাণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে বলে দাবি করেন।
ক্লদ লেভি-স্ট্রস দেখিয়েছেন মিথের চরিত্রগুলো বা ধারণাগুলো প্রায়ই একে অপরের বিপরীতে সংজ্ঞায়িত হয়। যেমন নারী/পুরুষ, প্রকৃতি/সংস্কৃতি, কালো/সাদা, আলো/আঁধার কিংবা কাঁচা/পাকা। এখানে এই বিপরীতগুলো অর্থ প্রদানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কাহিনীগুলোকে কাঠামোবদ্ধ করতে সহায়তা করে। ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম হতে গেলে শুরুতেই যেমন হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম বাঙালি কিংবা এই জাতীয় কিছু মিথ ও মিনিং তৈরি করতে হয়। তেমনি তার লেজ ধরে চলে আসে কিছু বিপজ্জনক বাইনারি অপোজিশন যেমন, মুক্তিযোদ্ধা/রাজাকার, প্রগতিশীল/মৌলবাদী, সংস্কৃতি/অপসংস্কৃতি, উন্নয়ন/গণতন্ত্র, রাতের ভোট/মেট্রোরেল, গুম-খুন-আয়নাঘর/পদ্মাসেতু, ব্যাংক ডাকাতি/ফ্লাইওভার প্রভৃতি তৈরি করা হয়েছিল। এখানে মিথ হিসেবে রাখা হয়েছিল হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি আর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিকে মিনিং হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছিল উপরে বর্ণিত ভুতুড়ে বাইনারি অপোজিশনগুলোকে।
বিভিন্ন ট্যাগসন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে যে ডিহিউম্যানাইজেশন তখন চলছিল সেগুলোকে জায়েজ করার ক্ষেত্রও প্রস্তুত করা হয়েছিল বাইনারি অপোজিশন থেকেই। আর সেজন্যই ফুঁকোর সেই টাওয়ার অব প্যানোপটিকন ভেঙ্গে পড়েছিল শিক্ষার্থী জনতার ‘তুমি কে আমি কে? রাজাকার! রাজাকার! শ্লোগানের মধ্য দিয়ে। তারপর উন্নয়নের প্রতীক হিসেবে ফ্যাসিবাদী আমলে প্রতিষ্ঠিত অবকাঠামোগুলোও নানামুখী আক্রমণের শিকার হয়। এই বিষয়গুলোকে আমরা রলাঁ বার্তের সেমিওটিক্স সামনে রেখে বিশ্লেষণ করতে পারি।
তিনি এই ধারণাটি প্রয়োগ করেছিলেন, এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিপরীতের সংযোজনের মাধ্যমে অর্থকে নাই করে দিয়ে ভিন্ন প্রতিমূর্তি তৈরি হয়। তার হিসেবে বাইনারি অপোজিশন হল ভাষা, মিডিয়া, এবং সমাজে অর্থ গঠন করার একটি প্রধান পদ্ধতি। তাই ফ্যাসিস্ট আমলের বাইনারিগুলোকে সবাই নায়ক/ভিলেন, সাদা/কালো কিংবা ভাল/খারাপ এর মতো বিপরীত জোড় হিসেবে মেনে নিয়েছিল। সাধারণত বিভিন্ন সাহিত্যের কাহিনি এবং চলচ্চিত্রের দৃশ্য কিংবা মিডিয়াতে পরিবেশিত সংবাদে যে বাইনারি অপোজিশন ব্যবহৃত হয়, যেখানে বাইনারির প্রতিটি দিক স্বতন্ত্র প্রতীকী মূল্য ধারণ করে। আর এগুলোই কাহিনি গঠনে সাহায্য করে।
আমরা জ্যাক দেরিদার ডিকন্সট্রাকশন সামনে রেখে দেখি। দেরিদা পশ্চিমি চিন্তায় বাইনারি অপোজিশনের ব্যবহার নিয়ে তুমুল সমালোচনা করেছিলেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই বিপরীতগুলো স্থির বা স্থিতিশীল নয়, বরং সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই বিপরীত জোড়গুলো শ্রেণিবদ্ধতা তৈরি করে। সেখানে এক দিককে অপরটির চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রাধান্য দেওয়া হয়। ডিকন্সট্রাকশনের মাধ্যমে, দেরিদা এই বিপরীত জোড়গুলো কীভাবে অস্থিতিশীল বা ‘অপসারণযোগ্য’ হতে পারে তা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি দাবি করেন বাইনারির কোন দিকই অপরটির চেয়ে স্বাভাবিকভাবে শ্রেষ্ঠ নয়।
দেরিদার মতো ফার্ডিনান্ড ডি সসুর এবং তার কাঠামোগত ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্বে আমরা দেখি ভাষায় অর্থ আসে পার্থক্যের সিস্টেমের মাধ্যমে। এখানে বাইনারি অপোজিশন এই সিস্টেমের একটি মূল অংশ। তিনি তাই প্রস্তাব করেছিলেন যে শব্দগুলো আসলে সংকেতকারী হিসেবে কাজ করে। তাদের মানে একে অপরের সাথে পার্থক্যের মাধ্যমে তৈরি করে, না তাদের নিজস্ব গুণাবলীর দ্বারা। উত্তর-ঔপনিবেশিকতা নিয়ে এডওয়ার্ড সাইদের যে বক্তব্য সেখানেও আমরা দেখি পশ্চিম প্রায়ই পূর্বকে ‘আদার’ তথা ‘অপরীকরণ’ করে বাদ দিচ্ছে। বাইনারি বিপরীত জোড়গুলো ঔপনিবেশিক শক্তির গতিশীলতাকে আরও শক্তিশালী করে। পাশাপাশি অ-পশ্চিমা সংস্কৃতির সম্পর্কে নেতিবাচক কল্পনার পাশাপাশি সেখানকার মানুষগুলোর ‘ডিহিউম্যানাইজেশনের ভিত্তি’ তৈরি করে। তারা পশ্চিমকে প্রায়ই যুক্তিসংগত, সভ্য, এবং অগ্রসর হিসাবে চিত্রিত করেছে। আর তার বিপরীতে পূর্বকে অযুক্তিসংগত, বর্বর, এবং পশ্চাৎপদ হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছে।
আমরা শুরু থেকে দেখে আসছি বাইনারি অপোজিশন ঔপনিবেশিক আধিপত্যকে বৈধতা দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। দিনের ভোট রাতের মধ্যে শেষ করে সিন্দাবাদের মতো আমাদের ঘাড়ে চেপে বসা ফ্যাসিবাদের পক্ষেও সম্মতি উৎপাদন করেছে এই বাইনারি অপোজিশন। তাইতো জুলাইয়ের বিপ্লবী শ্লোগানের একটি ছিল ‘বিকল্প কে? তুমি আমি’। এখানে কোনো বাইনারি বিকল্প না দেখে সরাসরি একে অন্যের পরিপূরক অবস্থানকে গুরুত্ব দিতে শিখিয়েছে জনতার ক্ষোভের তীব্র বহিঃপ্রকাশ থেকে। তাই আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, বাইনারি অপোজিশনগুলো ভাষা, সংস্কৃতি এবং চিন্তায় নতুন অর্থ গঠনের একটি শক্তিশালী পদ্ধতি যা জনদলনের হাতিয়ার হিসেবেও সুবিদিত। তাই যারা বুঝে কিংবা না বুঝে ‘উন্নয়ন নাকি গণতন্ত্র’ স্টাইলে ‘নির্বাচন নাকি সংস্কারের’ গল্প শোনাতে চাইছে তাদের আপাতত সন্দেহের চোখে দেখুন। সেই সঙ্গে দেড়যুগের পুরাতন প্রতিবাদ জারি থাক ‘আমরা আগে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার ফেরত চাই, সেইসঙ্গে উন্নয়নও চাই’। সংস্কার হচ্ছে হোক, সেইসঙ্গে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ একটি নির্বাচনও হতে হবে’। =