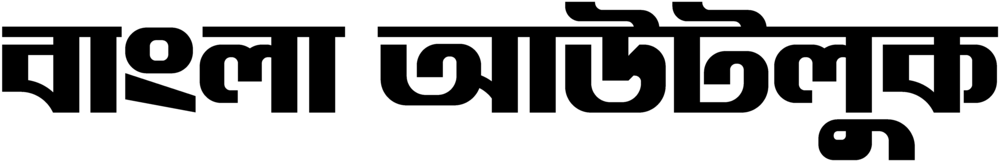-67e29038edee8.jpg)
প্রায় পনেরো বছর আগের কথা, ঢাকায় আসছি শুনে এক বন্ধু বললো, "চমৎকার, ওই সময়েই মেহেরজান মুক্তি পাবে, আমাদের সাথে প্রিমিয়ারে আসো ।"
"মেহেরজান?", আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জয়া বচ্চন এবং ভিক্টর ব্যানার্জি অভিনীত বড় পর্দার ১৯৭১এর প্রেক্ষিতে প্রেমের গল্প সম্পর্কে কিছুই না জেনে। পারিবারিক কারণে আমি সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারিনি। যারা যোগ দিয়েছিলেন, তারা সম্ভবত বাংলা ব্লগস্ফিয়ারের প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। পরিচালক রুবাইয়াত হোসেনের কি চরম আস্পর্ধা ! একজন বাঙালি মেয়ে একজন পাকিস্তানি সৈনিকের প্রেমে পড়েছে! সে - চরিত্র এবং পরিচালক উভয়ই - কি জানতো না যে যুদ্ধ চলছিল?
মেহেরজান নিয়ে শব্দ এবং ক্রোধ শর্মিলা বোসের "ডেড রেকনিং: মেমোরিজ অফ দ্য ১৯৭১ বাংলাদেশ ওয়ার" প্রতিক্রিয়ার তুলনায় অবশ্য হালকাই ছিল। চলচ্চিত্রটি যেখানে ছিল কল্পকাহিনি, বইটি ছিল একটি গবেষণার ফসল। বোস, একজন অক্সফোর্ড গবেষক, ১৯৭১ পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা সংগঠিত পূর্ব-পরিকল্পিত গণহত্যার প্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক বাংলাদেশি বর্ণনাগুলোকে প্রশ্ন করেছিলেন - প্রশ্ন তুলেছিলেন আসলেই কোনো গণহত্যা ঘটেছিল কি না।
বোসের দাবিগুলোর সাথে বৌদ্ধিকভাবে মোকাবিলা করার পরিবর্তে, অনেক বাংলাদেশি ও বাংলাভাষী গবেষক অনানুষ্ঠানিক, সোশ্যাল মিডিয়া আক্রমণে জড়িত হয়েছিলেন। ব্যতিক্রম ছিলেন আখতারুজ্জামান মন্ডল, নয়নিকা মুখার্জী, দীনা সিদ্দিকী, আফসান চৌধুরী, উর্বশী বুটালিয়া, এবং নাঈম মোহাইমেন। "দ্য ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি"তে কলম্বিয়া নৃবিজ্ঞানী মোহাইমেনের প্রবন্ধ এবং একই জার্নালে বোসের জবাবে মোহাইমেনের ফলো-আপ প্রতিক্রিয়া এখন পর্যন্ত বোসের থিসিসের সবচেয়ে কার্যকর খণ্ডন।[১]
গত পনেরো বছরে, যখন দেশের ভেতর ১৯৭১ নিয়ে সরকারি বয়ানের বাইরে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিদেশে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। এই সিরিজটি গ্যারি জে বাস, শ্রীনাথ রাঘবন, এবং সলিল ত্রিপাঠী লিখিত সেরকম তিনটি বই নিয়ে। মুক্ত দেশে, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে, এই বইগুলো পড়লে - এবং সেখানে যা আছে এবং যা নেই তা নিয়ে ভাবলে - যে ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে সেগুলো বুঝতে সুবিধা হবে।
এই সিরিজটি কোনোভাবেই ১৯৭১ সালের একটি সম্পূর্ণ সাহিত্য পর্যালোচনা নয়। বাংলাদেশের সৃষ্টির বিশেষ দিকগুলো নিয়ে কিছু মূল বই এবং কাজ - অর্থনৈতিক কারণ এবং পরিণতি, শরণার্থী প্রবাহ, সাম্প্রদায়িক এবং জাতিগত মাত্রা, লিঙ্গ সহিংসতা - নিয়ে কিছু বলছি না, কারণ এগুলো নিয়ে বাস, রাঘবন, এবং ত্রিপাঠী লেখেননি। তবে, এই তিনটি বই পর্যালোচনা করার সময়, ১৯৭১ সালের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজগুলোও আলোচনা করা হবে ।
বেশিরভাগ নন-ফিকশন পর্যালোচনার একটি ফর্মুলা আছে - লেখক ক খ গ নিয়ে লিখেছেন, কিন্তু প ফ ব নিয়ে লেখেননি। উদাহরণস্বরূপ, WDW রিভিউ ("দ্য জিঞ্জার মার্চেন্ট অফ হিস্টরি") এর একটি পরবর্তী প্রবন্ধে এই নতুন বইগুলোর তার পর্যালোচনায়, মোহাইমেন সিদ্ধান্ত দেন যে - “History’s ‘ginger merchant’ was far more crucial in the build up and conduct of this war than is acknowledged…”[২]
Ginger merchant - আদার ব্যাপারি - প্রবাদপ্রতিম বাঙালি ছোট ব্যবসায়ী যিনি সম্ভবত বিশ্ব পুঁজি নির্ধারিত সবকিছুর প্রতীকী সমুদ্র জাহাজগুলো সম্পর্কে অবহিত নন। ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটে, মোহাইমেন দাবি করেন যে “… the radical leftist guerilla, or the desperate peasant fighter are the ginger merchants who constituted turbulent street forces that made crucial differences to the fateful negotiations”।
যে কোনও পর্যালোচনা যদি কি অনুপস্থিত তা নিয়ে বিবেচনা করে, সেটা যা পর্যালোচনা করা হচ্ছে তা সম্পর্কে যতটা বলে, ততটাই বলে পর্যালোচক সম্পর্কে । এই সিরিজটিও বইগুলো থেকে কী অনুপস্থিত থাকতে পারে তা বলার প্রবণতা থেকে মুক্ত নয়। তবুও, আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখতে, আমি দুটি প্রশ্ন নিয়ে লিখতে যাচ্ছি: লেখক আমাদের কি বলতে প্রস্তাব করেন যা আমরা বিদ্যমান রচনা থেকে জানতাম না; এবং লেখক কি আসলে তিনি যা প্রস্তাব করেন তা আমাদের বলতে সক্ষম হন?
রিচার্ড সিসন এবং লিও ই রোজের "ওয়ার অ্যান্ড সিসেশন: পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, অ্যান্ড দ্য ক্রিয়েশন অফ বাংলাদেশ" বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সম্ভবত ইংরেজিতে সবথেকে মৌলিক কাজ। লেখকগণ (বইটি প্রকাশিত হওয়ার সময় যথাক্রমে UCLA এবং বার্কলে থেকে) ১৯৭১ সালের যমজ সংকটের মূল খেলোয়াড়দের -- মার্চে সামরিক ক্র্যাকডাউনের দিকে নিয়ে যাওয়া পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ এবং সামরিক শাসকরা; এবং ডিসেম্বরে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধের আগে ভারতীয় এবং পাকিস্তানি সরকার -- সিদ্ধান্তের পিছনে অভিপ্রায় এবং হিসাবগুলো বুঝতে চান ।
বইটি ১৯৭০-এর দশকের শেষের দিকে পরিচালিত বিস্তারিত সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে। ভারতীয়দের মধ্যে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী, তার মূল মন্ত্রীরা, এবং সংকট পরিচালনার দায়িত্বে থাকা শীর্ষ আমলাদের। পাকিস্তানি দিক থেকে, ইয়াহিয়া খান প্ৰশাসনের সমস্ত মূল খেলোয়াড়, জেনারেল নিজেসহ, এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল এএকে নিয়াজি এবং মেজর জেনারেল রাও ফারমান আলীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত ছিলেন জেড এ ভুট্টো, যিনি জিয়া-উল হক দ্বারা ফাঁসির অপেক্ষায় ছিলেন , এবং জেনারেল টিক্কা খান, যিনি সেই সময়ে জেলে ছিলেন।
সেই সময়ে, সাবেক পাকিস্তানের অন্য অংশটিও জিয়া নামে একজন সামরিক ব্যক্তি দ্বারা শাসিত হচ্ছিলো। তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়নি, কিন্তু নেওয়া হয়েছিল মুক্তিবাহিনীতে তার কমান্ডার জেনারেল এমএজি ওসমানীর সাক্ষাৎকার । আরো ছিলেন মার্চ ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের একজন মূল সহায়ক কামাল হোসেন। শেখ মুজিবুর রহমান ততদিনে নিজেই দীর্ঘদিন মৃত, মৃত তাজউদ্দিন আহমেদ। অর্থাৎ, দশক শেষ হওয়ার আগেই, সেই ঘটনাবহুল বছরের সিদ্ধান্তের পিছনে তাদের অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করার জন্য কিছু মূল খেলোয়াড় ইতিমধ্যেই অনুপস্থিত ছিলেন।
এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেখানে আমরা ফিরে আসব।
সাক্ষাৎকারগুলোর ওপর ভিত্তি করে সিসন এবং রোজ বিশ্বস্তভাবে ১৯৭১ সালের বসন্তের ঘটনাগুলো পুনর্নির্মাণ করেন। তারা দাবি করেন যে যদিও তিন প্রধান খেলোয়াড় - ইয়াহিয়া, ভুট্টো, এবং মুজিব - একটি সংযুক্ত পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে সামরিক আইনের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তির চেয়েছিলেন, কীভাবে তা হবে সেটা নিয়ে তিনজনেরই আলাদা আলাদা ধারণা ছিল, এবং প্রত্যেকে মৌলিকভাবে অন্য দুজনকে ভুল বুঝেছিলেন। লেখকদের বর্ণনায় পাকিস্তানি জেনারেলদের খুবই খারাপভাবে দেখা যায়। শুধুমাত্র তাদের জাতিবাদী বাঙালিবিরোধী পক্ষপাত এবং রাজনীতিবিদদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মনোভাব নয়, লেখকরা দেখান যে সেনা শাসকদের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরে আলোচনার জন্য কোন গুরুতর প্রস্তুতি ছিল না, বিশেষ করে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, তারা সম্পূর্ণরূপে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা প্রতি মনোভাব বুঝতে পারেনি, তারা বিশ্বাস করেছিল যে আওয়ামী লীগ প্রধান উচ্চ পদের লোভের জন্য তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ফেলে দেবেন।
আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পরে, জেনারেলরা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন যে পাকিস্তান সহজেই জয়ী হবে। অবশ্যই, যুদ্ধ যেভাবে তারা ভেবেছিল সেভাবে হয়নি। ভারত অনিবার্যভাবে আরও জটিলভাবে জড়িত হওয়ার সাথে, লেখকদ্বয় দেকাচ্ছেন যে ইয়াহিয়া প্রশাসন আবারও পরিস্থিতি ভুলভাবে পড়েছে। পাকিস্তান বিশ্বাস করেছিল যে পরাশক্তিগুলো দ্রুত হস্তক্ষেপ করবে। অন্যদিকে, লেখকদের মতে , ভারতীয় নেতৃত্ব বাস্তবতার উপর অনেক ভাল দখল রাখতে পেরেছে। ভারতীয়রা বুঝেছিল বাংলাদেশিদের দীর্ঘ যুদ্ধ লড়ার প্রস্তুতির অভাব এবং ভিয়েতনাম এবং বায়াফ্রাতে যুদ্ধ চলাকালীন অন্য যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু করার জন্য পরাশক্তিগুলোর অনিচ্ছা ।
লেখকরা দেখান যে, এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় যে ভারত ডিসেম্বরে জিতেছিল। কিন্তু লেখকরা আরো দেখান যে পাকিস্তানিরাই লড়াই নিয়েছিল, আবার, অন্য পক্ষকে সম্পূর্ণরূপে ভুলভাবে পড়ে।
সিসন আর রোজ এর এই গল্পে অনেক কিছু অনুপস্থিত থাকলেও - মোহাইমেনের আদার ব্যাপারী এবং মৃত নেতাদের স্মরণ করুন - ১৯৭১ সাল সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তাতে হাবুডুবু খাওয়া ব্লান্ডারিং জেনারেলদের স্ট্যান্ডার্ড গল্প চ্যালেঞ্জ করা হয় না।
তাহলে, বাস, রাঘবন, এবং ত্রিপাঠী আমাদের এর বাইরে কী বলেন?
(দ্বিতীয় পর্বে বাস এর বই নিয়ে আলোচনা)
[1] Naeem Mohaiemen, “Flying blind: waiting for a real reckoning on 1971”, Economic and Political Weekly, 2011.
[2] Naeem Mohaiemen, “The Ginger Merchant of History (Standing in the shadow of “Giants”)”, Witte de With Review, Sediments, Nov. 2016. Reprinted in WdW Review: Arts, Culture and Journalism in Revolt, Vol. 1 (2013 – 2016), 2017.
● Dead Reckoning: Memories of the 1971 Bangladesh War by Sarmila Bose, C Hurst & Co, 2011.
● War and Secession: Pakistan, India, and the Creation of Bangladesh by Richard Sisson and Leo Rose, University of California, 1991.
Jyoti Rahman is a Bangladeshi writer. His pieces are archived www.jrahman.substack.com-
জ্যোতি রহমান, অর্থনীতিবিদ